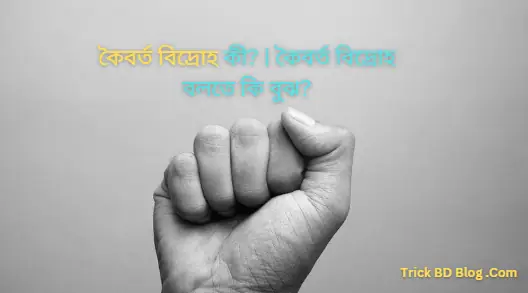’মেঘনাদবধ কাব্য’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত।
তবে অনেকেই ‘মেধনাদবধ কাব্য’ কে মহাকাব্যের লক্ষ বিচারে মহাকাব্য বলা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
তবে সমালোচকগণ এই কাব্য নিয়ে যত সমালোচনা করে থাকুক না কেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।
পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী এই মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্যের শিল্প সৌদর্য লাভ করেছে।
ঘটনার একমুখীনতা এর একটি পাশ্চাত্য মহাকাব্যেই অনেকটা সমধর্মী বলে স্বভাবত মনে হতে পারে, মধুসূদন তাঁর কাব্যে ঘটনা ও চরিত্রের সাথে সাথে ভাব, ভাষায়, ছন্দে ও অলঙ্কারে যে গৌরব ও গাম্ভীর্য থাকা আবশ্যক তা রক্ষা করায় যত্নশীল ছিলেন।
এই কাব্যে কবির মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কল্পনা ও বর্ণনা শক্তির মধ্যে যা মহাকাব্যের অনুকূল বলে বিবেচনা যোগ্য।
এই মেঘনাদবধ কাব্যে রূপলাভ করেছে পাশ্চাত্য কাব্যকলা এবং এতে আরোপিত হয়েছে বিষয় উপযোগী ছন্দ।
এ কাব্যের উপযোগিতা যুগিয়েছে পৌরাণিক কাহিনি। এতে প্রতিফলিত হয়েছে বীর চরিত্রের গৌরব, মেঘনাদবধ কাব্য যুগজিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়ে হয়ে উঠেছে সার্থক মহাকাব্যের দাবিদার।
মহাকাব্য কাকে বলে?
ইংরেজি Epic শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে মহাকাব্য। এই Epic শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Epos থেকে, যার অর্থ ‘শব্দ’। পরবর্তী সময়ে Epos বলতে, সঙ্গীত, কাহিনি, বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা ইত্যাদি বোঝাতো। তবে Epic বলতে এখন বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিমূলক কবিতা বুঝিয়ে থাকে।
আসলে মহাকব্য বলতে যে অতিকায় কবিকৃতি বোঝানো হয় তা একথায় তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অসম্ভব।
এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টে ভিন্নতা বিদ্যমান রয়েছে কারন, এই সুপ্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টি প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে স্বাতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।
বিশেষ কয়েকটি লক্ষণযুক্ত কাব্যকে প্রাচ্য তথা সংস্কৃত আদর্শ অনুযায়ী মহাকাব্য বলে অভিহিত করা হয়।
মহাকাব্যের বৈশিষ্ট
নিচে মহাকাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট তুলে ধরা হলো:
মহাকাব্যের নায়ক হবেন চতুর ও উদার এবং নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণ সম্বলিত, সদ্বংশজাত কোনো ক্ষত্রিয়। এখানে দেবতাও নায়ক হতে পারেন।
নমস্কার, আশীর্বাদ বা বস্তুনির্দেশ দ্বারা মহাকাব্য আরম্ভ হবে।
মহাকাব্য ইতিহাস বা কোনো সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা হবে।
মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গযুক্ত সর্গ বিভাগ থাকবে। অর্থাৎ আট এর কম হবে না সর্গ সংখ্যা এবং সর্গ খুব ছোট বা খুব বড় হবে না। সমগ্র সর্গই একই ছন্দে রুচতত হবে এবং সর্গান্তে পরিবর্তন ঘটবে ছন্দের। সেই সাথে পরবর্তী সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া থাকবে প্রত্যেক সর্গের শেষে।
চতুর্বর্গ ধর্ম, কা, অর্থ ও মোক্ষ ফল লাভ হবে মহাকাব্য থেকে।
মহাকাব্য হবে অলঙ্কার ও রসভার সম্ভলিত। তবে এই রস শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত যেকোনো একটি প্রাধান্য পাবে।
মহাকাব্যে যেসব বিষয়ের বর্ণনা থাকবে তা হলো: নগর, পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্রসূর্য উদয়, মধুপান, জলক্রীড়া, বিপ্রলম্ভ, যুদ্ধ, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ের।
মহাকাব্য হিসেবে মেঘনাদবধ কাব্যের সার্থকতা
মেঘনাদবদ কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে বিবেচিত। তবে মেঘনাদবধ কাব্যকে মহাকাব্যের লক্ষণবিচারে সার্থক মহাকাব্য বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আক্ষেপই করেছেন,
”বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোনো প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব। তারপর কত হাজার বৎসর অতীত হয়ে গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হল না। ‘গাইব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত’ বলে কবি মহাকাব্যের ঘোষণা দিয়েছেন অথবা Let me write a few Epiclings বলে বিষয়টিকে হাল্কা করার চেষ্টা করেছিলেন বলা দুষ্কর। আবার এক চিঠিতে তিনি এমন কথাও লিখেছিলেন যে, সুনিপুণ ফরাসি সমালোচক ও তাঁর মহাকাব্যে কোনো দোষ দেখাতে পারবেন না। কবির মন্তব্যের লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। তবে এই মর্যাদা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো আদর্শানুসারী তা বিবেচনা অপেক্ষা রাখে।”
প্রাচ্যের ধারণা:
মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। মহাকাব্য সে হিসেবে হবে ইতিহাস, পুরান বা পুরাবৃত্তের ঘটনা অবলম্বনে অষ্টাধিক সর্গ সংখ্যা সম্বলিত।
মহাকাব্যের নায়ক হবেন দেবত বা সদ্বংশোদ্ভূত নরপতি এবং মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে নায়কের জয় বা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রসারী হবে কাহিনি এবং বলা হয়েছে বিশেষ ছন্দে রচিত মহাকাব্যের সুনির্দিষ্ট রসের কথাও।
প্রাচ্য অলঙ্কারিকগণ এ ধরনের কিছু বাধ্যবাধকত মেনে মহাকাব্য রচনার নির্দেশ জারি করেছেন।
মেঘনাদবধ কাব্যের অবতারণা:
প্রাচ্য আদর্শ মেনে চলেননি মুধুসূদন। তাঁর কাব্যের পরিসমাপ্তি নায়কের বিজয় বা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘটেনি। সেই সাথে মানা হয়নি ছন্দের আলঙ্কারিক নির্দেশও। এখানে উপেক্ষিত হয়েছে চতুর্বর্গ ফল লাভের ব্যাপারটিও।
মহাকাব্যের বাইরের পরিচয় এই প্রাচ্য আদর্শের সংজ্ঞঅ স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে, এতে মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ বা প্রকৃত পরিচয় বিবৃত হয়নি।
এই সংজ্ঞার গুরুত্বহীনতার কথা বিবেচনা করে হয়ত মধুসূদন মন্তব্য করেছিলেন যে,
‘I will not allow myself to e boand by the dicta of Mr. Viswana the of sahitya Darpan. I shall look to the greatest drama lists of Europe for models.’
তবে মধুসূদন প্রাচ্য অলঙ্কারিক বিশ্বনাথের নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না চাইলেও যে তা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন এমন দবিও করা যায় না।
কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে নয়টি সর্গে, এই কাব্যে বীর ও করুণ রসের উপস্থিতি বর্তমান। এ কাব্যে অনেকাংশেই প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করা হয়নি। তাই সেই মাপকাঠিতে বিচার করে এই কাব্যকে মহাকাব্য নামে অভিহিত করা সমীচীন নয় বলে অনেকে ধারণা করেন।
কিন্তু এই নিরিখে বিচার করা উচিত হবে না মেঘনাদবধ কাব্যকে, কারন কবির পাশ্চাত্য আদর্শের গৌরব ঘোষণা করেছেন এবং পশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রতি তাঁর অনেক বেশি আনুগত্য ছিল।
অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বহিরঙ্গেরই প্রাধান্য পেয়েছে প্রাচ্য আদর্শের যে স্বরূপ লক্ষ করা যায় তাতে। মহাকাব্য বিচারের মাপকাঠি বাইরের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অভ্যন্তরীণ স্বরূপ লক্ষণই হওয়া দরকার বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
এবং মেঘনাদবধ কাব্যকে সেদিক থেকেই বিবেচনা করা আবশ্যক।
আরও পড়ুন:
- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়?
- পড়াশোনায় মনোযোগ আনার ১০টি কার্যকরী উপায়
- ছয় দফা কর্মসূচী আসলে কি? ছয় দফা কর্মসূচীর দফা ছয়টি কি কি?
- সামজিক অসমতা বলতে কি বুঝায়?
কাব্যের বিষয়বস্তু:
মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রের সমুন্নতি, বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য, ভাবের গাম্ভীর্য, বর্ণনার নাটকীয়তার সাথে কাব্যকলার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাতে এমন মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত দাবি নেই যে এতে মহাকাব্যের গৌরবের কোনো অভাব ঘটেছে।
বরং মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী যাকে লিটারেরি এপিক বলে অভিহিত করা হয় তার সাথে যথেষ্ট সঙ্গতি রয়েছে।
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, ‘এর বহিরঙ্গ গঠনের মধ্যে ও পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী মহাকাব্যের শিল্পসৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে, এর চরিত্রগুলোর মধ্যেও নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়া মধ্যে মধ্যে চমৎকারিত্ব ও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।”
মধুসূদন ঘটনা ও চরিত্রের সাথে সাথে ভাবে ভাষায় ছন্দে ও অলঙ্কারে যে গৌরব ও গাম্ভীর্য থাকা আবশ্যক তাঁর কাব্যে তা রক্ষা করায় যত্নশীল ছিলেন।
রাক্ষসদের নায়ক দের করার মধ্যে যে ক্রটি আছে বলে ধারণা করা হয় তা যাথার্থ নয়। কারন রাক্ষসদের অসভ্য, বর্বর বলে চিত্রিত করেননি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাদের সুসভ্য বীর জাতি হিসেবেই দেখানো হয়েছে।
কবি মূলত মানবিকতার জয়গান ঘোষণা করেছেন রাক্ষস বীর্যবতার অন্তরালে। যে ধরনের কাব্য পাঠ করলে পাঠক মহল বিস্মিত, উত্তেজিত, স্তম্ভিত ও অশ্রুশিক্ত হয়ে বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করে তাকে মহাকাব্য বলা যায়।
পরিশেষে বলা যায় যে, কেউ কেউ মনে করেন যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির কঠোর সংযম নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিবর্তে গীতিকাব্যের হৃদয়াবেগ ও পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন ফুটে উঠেছে। অনেকে আন্তর প্রকৃতিতে মেঘনাদবধ হীতিকাব্য হয়ে উঠেছে বলেও মনে করে থাকেন।
কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিস্ময়কর প্রতিভার অবদান হিসেবে এক অভিনব সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা যায়। যার ফলে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবে বাংলা মহাকাব্যের ধারায় মেঘনাদবধ কাব্য বিরাজমান।
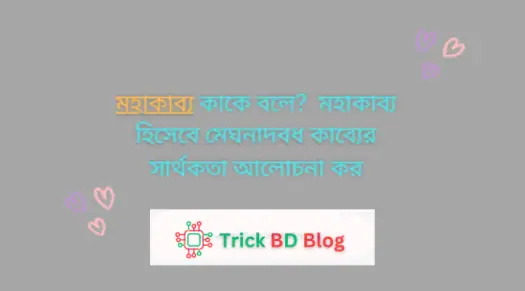
![বারমাসী বা বারমাস্যা বলতে কী বুঝ? [ বিস্তারিত ]](https://trickbdblog.com/wp-content/uploads/2024/05/Screenshot_300.webp)